প্রবন্ধ
রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল
 শুভাশিস মল্লিক
শুভাশিস মল্লিক
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন শান্ত, স্থিতধী। অনেকটা প্রাচীন বটবৃক্ষের মতো। যার ছায়ায় আমরা স্নিগ্ধ হই। প্রশান্তি লাভ করি। অপরদিকে কাজী নজরুল ইসলাম হলেন চির চঞ্চল, ধূমকেতুর মতো। ধূমকেতুর মতোই আগমন, ধূমকেতুর মতোই বিচরণ। বংশ গরিমা থেকে আরম্ভ করে শিক্ষাদীক্ষা, জীবন যাপন প্রভৃতি অনেক বিষয়েই দু’জনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তবু বাংলা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অনেকে রবীন্দ্র – নজরুল নামদু’টি একসঙ্গে উচ্চারণ করেন। এমনকি অনেক জায়গায় ‘রবীন্দ্র – নজরুল সন্ধ্যা’ও পালিত হয়। এখন এই আলোচনায় দু’জনের মধ্যে সম্পর্কটা ঠিক কেমন ছিল সেটা একটু দেখে নেওয়া যাক।
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের প্রথম সাক্ষাৎ ঠিক কবে হয়েছিল সেই নিয়ে মতভেদ আছে। তবে সবথেকে প্রামাণ্য তথ্য অনুযায়ী দু’জনের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে। রবীন্দ্রনাথ তখন খ্যাতির শীর্ষে অবস্থান করছেন। তাই তাঁর সঙ্গে দেখা করার এক অদম্য বাসনা নিয়ে নজরুল যে শান্তিনিকেতনে ছুটে যাবেন সে ব্যাপারে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এবং জানা যায় এই প্রথম সাক্ষাতের সময় নজরুল তাঁর সদ্য রচিত ‘আগমনী’ কবিতাটি আবৃত্তি করেন। পরে নজরুল তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ নাকি তাঁকে শান্তিনিকেতনে থেকে সেখানকার ছাত্রদের শরীরচর্চার তদারকি করার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে গান শেখার জন্যও বলেছিলেন।
এই কথাগুলি থেকে রবীন্দ্রনাথ তখন নজরুল সম্বন্ধে কী ধারণা পোষণ করেছিলেন সে বিষয়ে একটা আন্দাজ করা যায়। কিন্তু কথাগুলি অন্যভাবে নিলে অন্যায় করা হবে। কেননা নজরুল তখনও নজরুল হয়ে ওঠেননি। এমনকি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা ‘বিদ্রোহী’ও তখনও প্রকাশিত হয়নি। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ তখন বিদেশে এক বছরেরও বেশি কাটিয়ে সদ্য দেশে ফিরেছেন। তাই নজরুলের কাব্য প্রতিভা সম্বন্ধে তাঁর কোনও ধারণা না থাকারই কথা। এবং সংগীত প্রতিভায় নজরুল যে অন্য অনেকের থেকে বড় হয়ে উঠবেন সেটাও আন্দাজ করতে পারেননি।
আস্তে আস্তে অবশ্য যত দিন যায় রবীন্দ্রনাথ ততই নজরুল সম্পর্কে অবহিত হন এবং তাঁর কাব্য প্রতিভা নিয়েও উচ্ছ্বসিত হন। ধীরে ধীরে তাঁদের মধ্যে এক সুসম্পর্কও গড়ে ওঠে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দু’জনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মত প্রকাশের মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল। যেমন রবীন্দ্রনাথ গরিব মানুষদের নিয়ে অনেক গল্প কবিতা লিখেছেন এবং নিজের জমিদারিতে দরিদ্র প্রজাদের মঙ্গলের জন্য অনেক পরিকল্পনাও নিয়েছিলেন। কিন্তু ‘দারিদ্র্য’কে সাহিত্যে একটা চমক হিসেবে ব্যবহার করাটাকে তিনি সমর্থন করেননি। বস্তুত তাঁর মত ছিল নতুনত্ব আর আধুনিকতা এক জিনিস নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন, “অন্যান্য সকল বেদনার মতোই সাহিত্যে দারিদ্র্যবেদনারও যথেষ্ট স্থান আছে। কিন্তু ওটার ব্যবহার একটা ভঙ্গিমার অঙ্গ হয়ে উঠেছে – যখন-তখন সেই প্রয়াসের মধ্যে লেখকেরই শক্তির দারিদ্র্য প্রকাশ পায়।”
অপর দিকে নজরুল দারিদ্র্যের মধ্যেই বেড়ে উঠেছিলেন। তিনি যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন, তাতে দারিদ্র্য শুধু ভঙ্গিমারই অঙ্গ ছিল না, বরং তাঁর কোনও কোনও কবিতায় দারিদ্র্যই ছিল মূল বিষয়বস্তু। এমনকি ‘দারিদ্র্য’ কবিতায় তো তিনি দারিদ্র্যকে রীতিমতো গৌরবান্বিত করেছিলেন। “হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে ক’রেছ মহান! / তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান / কন্টক-মুকুট শোভা! দিয়াছ, তাপস, / অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস; / উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি, বাণী ক্ষুরধার, / বাণী মোর শাপে তব হ’ল তরবার!”
সাহিত্যের নতুন আঙ্গিগ, ভাষা প্রভৃতি নিয়ে যে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল, তা চরম আকার ধারণ করে ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে দেওয়া এক সংবর্ধনা সভায় রবীন্দ্রনাথ রক্ত অর্থে ‘খুন’ শব্দ ব্যবহার করার সমালোচনা করেন। ‘খুন’ শব্দটিকে তিনি শুধুমাত্র হত্যা করার অর্থে ব্যবহার করারই পক্ষে ছিলেন। এই বিরোধিতার কারণ ঠিক বোঝা যায় না। কারণ সাহিত্যে একই শব্দ বিভিন্ন রকম অর্থে ব্যবহার করা যেতেই পারে। এমনকি রবীন্দ্রনাথ নিজেও বহু নতুন শব্দ সৃষ্টি করেছেন।
এখন এই ‘খুন’ শব্দটা নজরুল তাঁর সাহিত্যে প্রায়শই ব্যবহার করতেন। বস্তুত এটা তাঁর একটা প্রিয় শব্দ ছিল। কাজেই তাঁর মনে হল রবীন্দ্রনাথ হয়তো তাঁকে উদ্দেশ করেই এই কথাটা বলেছেন। তাঁর অভিমান হল, রাগ হল। এমনকি সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করে ‘বড়র পিরীতি বালির বাঁধ’ নামে একটা প্রবন্ধও লিখে ফেলেন। এই প্রবন্ধে তিনি এটাই বলতে চেয়েছেন যে, ছাত্র জীবন থেকেই তিনি রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথও তাঁকে অত্যধিক স্নেহ করেন। ‘খুন’ শব্দটির ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি বাংলা সাহিত্যে আরবি-ফারসি ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাঁর বহু রচনায় এইরকম আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার করেছেন। তাঁর মনে হয়েছিল যে, সম্ভবত যারা শুধু বিদ্রূপ কিংবা গালিগালাজ করে তারা এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করেছে। কিন্তু “বিশ্বকবি-সম্রাটের আসন – রবিলোক – কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির বহু ঊর্ধ্বে।”
যাইহোক, বিতর্কটা যাতে আর না বাড়ে সেজন্য এগিয়ে আসেন প্রমথ চৌধুরী। তিনি ‘বঙ্গ-সাহিত্যে খুনের মামলা’ নামে একটি প্রবন্ধে লেখেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতায় নজরুলের সমালোচনা করেননি। কোনও উদীয়মান কবির নবীন ভাষার উদাহরণ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ‘খুন’ শব্দটির উল্লেখ করেছেন। আর নজরুল মোটেই উদীয়মান কবি নন, বরং তিনি উদিত কবি। তাঁর এই লেখাটি প্রকাশিত হবার পর এই নিয়ে প্রকাশ্যে অন্তত বিতর্কটা আর বেশিদূর গড়ায়নি।
মানুষ স্বভাবতই আবেগপ্রবণ। কবি সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে কথাটা আরও বেশি করে প্রযোজ্য। তাই দু’জনের মধ্যে মান অভিমান থাকলেও তা ছিল সাময়িক। রবীন্দ্রনাথ যেমন নজরুলকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, ঠিক তেমনই নজরুলও রবীন্দ্রনাথকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করতেন। বস্তুত তাঁকে গুরুদেবের আসনে বসিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে প্রশস্তিমূলক বহু কবিতা এবং গান তিনি রচনা করেছিলেন। ‘আজি হতে শতবর্ষ আগে’ নামক কবিতা লিখে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাও নিবেদন করেন। এমনকি তাঁর কবিতা সংকলন ‘সঞ্চিতা’ গ্রন্থটি তিনি উৎসর্গও করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকেই। উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন, ‘বিশ্বকবিসম্রাট্ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু’।
নজরুল বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনা করেছিলেন। তার মধ্যে একটি ছিল রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’। কিন্তু এই ছবিতে রবীন্দ্রনাথের গানগুলি শুদ্ধরূপে গাওয়া হয়নি বলে বিশ্বভারতী আপত্তি শুরু করে। নজরুল তখন চলচ্চিত্রের ফিল্ম আর প্রোজেক্টর নিয়ে সটান শান্তিনিকেতনে গিয়ে হাজির হন এবং রবীন্দ্রনাথকে গানগুলি শোনান। রবীন্দ্রনাথ গানগুলির মধ্যে আপত্তির কিছুই খুঁজে পাননি। বরং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কোনও আপত্তি নেই বলে সই করে দেন।
নজরুল যখন ‘ধূমকেতু’ পত্রিকা সম্পাদনার কাজ শুরু করেন, তখন ঠিক করেছিলেন বেশ কিছু বিখ্যাত ব্যক্তির শুভেচ্ছাবাণী ছাপবেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিরাশ করেননি। তাঁর একটি শুভেচ্ছাবাণী এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।
রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে ঠিক কী চোখে দেখতেন তার আরও একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নজরুল যখন আলিপুর জেলে বন্দি ছিলেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর সদ্য প্রকাশিত বসন্ত গীতিনাট্যটি নজরুলকে উৎসর্গ করেছিলেন। বয়সের দিক থেকে তরুণ হলেও নজরুল যে অসামান্য প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ সে কথা ঠিকই বুঝেছিলেন। এই ঘটনা সেটাই প্রমাণ করে। আবার নজরুলের দিক থেকেও এটা একটা অভাবনীয় ব্যাপার ছিল। ছোটবেলা থেকে তিনি যাকে প্রায় পুজো করে এসেছেন, সেই বিশ্বকবি তাঁকে একটা বই উৎসর্গ করেছেন, এর থেকে বড় পুরস্কার তাঁর কাছে আর কিছুই হতে পারে না।
আবার নজরুল যখন জেলে অনশন করছেন, তখন তাঁর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অনশন তুলে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করে একটা টেলিগ্রাম করেছিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন, “Give up hunger strike, our literature claims you”. যদিও দুর্ভাগ্যবশত টেলিগ্রামটি নজরুলের হাতে এসে শেষপর্যন্ত পৌঁছয়নি।
কে বড়, কে ছোট তা নির্ণয় করা, কিংবা কে ঠিক কে ভুল সেই বিতর্ক উসকে দেওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। একটা কথা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। সেটা হল দু’জনেই রক্ত মাংসের মানুষ ছিলেন। তাই তাদের মধ্যে ছোটখাটো রাগ, মান অভিমান থাকতেই পারে। কিন্তু সেগুলোকে দিয়ে তাদের বিচার করাটা ভুল হবে। বরং এটাই সত্য যে, তাদের সম্পর্ক স্নেহ, ভালোবাসা, শ্রদ্ধায় এক দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্যন্ত এই বন্ধন অটুট ছিল।
জাগতিক নিয়মেই রবীন্দ্রনাথকেও একদিন মৃত্যুর কাছে হার মানতে হয়েছিল। তাঁর শেষযাত্রার ধারাবিবরণী কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করার ব্যবস্থা করা হল। নজরুলকে দিয়ে একটা তাৎক্ষণিক শোকগাথা লেখানো হল এবং তাঁকে দিয়ে সেটা পাঠও করানো হল। নজরুল লিখলেন- “দুপুরের রবি পড়িয়াছে ঢলে অস্তপথের কোলে / স্রাবণের মেঘ ছুটে এল দলে দলে/ উদাস গগনতলে,/ বিশ্বের রবি ভারতের কবি/ শ্যাম-বাংলার হৃদয়ের ছবি/ তুমি চলে যাবে বলে। …” (রবিহারা)
নজরুল এর আগে অনেকবারই বিশিষ্ট মানুষদের জীবনাবসানে তাৎক্ষণিক শোকগাথা লিখেছেন। কিন্তু ইনি তো তাঁর গুরুদেব! এ তো শুধু তাগিদের জন্য লেখা নয়। এই লেখার মধ্যে দিয়ে তো তাঁর অন্তরের গভীর বেদনাই প্রকাশ পেয়েছে। আর সেজন্যই তো কবিতাটা পাঠ করার সময় বারবার তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিল। পাঠটি শেষও করে উঠতে পারেননি। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সেটি শেষ করেছিলেন।
প্রায় একই সময়ে নজরুল রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আর একটি কবিতা রচনা করেন।
“ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে, জাগায়ো না জাগায়ো না,/ সারা জীবন যে আলো দিল, ডেকে তার ঘুম ভাঙায়ো না। …”(রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত শোককবিতার অন্তর্গত – ২৭ সংখ্যক; বুলবুল ২য়) ।
আশা করি এই দু’টি ঘটনার মধ্যে দিয়েই তাঁদের সম্পর্কের স্বরূপটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। ♥
কৃতজ্ঞতা স্বীকার – বিদ্রোহী রণক্লান্ত নজরুল – জীবনী – গোলাম মুরশিদ
নজরুল জীবনী – অরুণকুমার বসু
শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
সঞ্চিতা – নজরুল ইসলাম

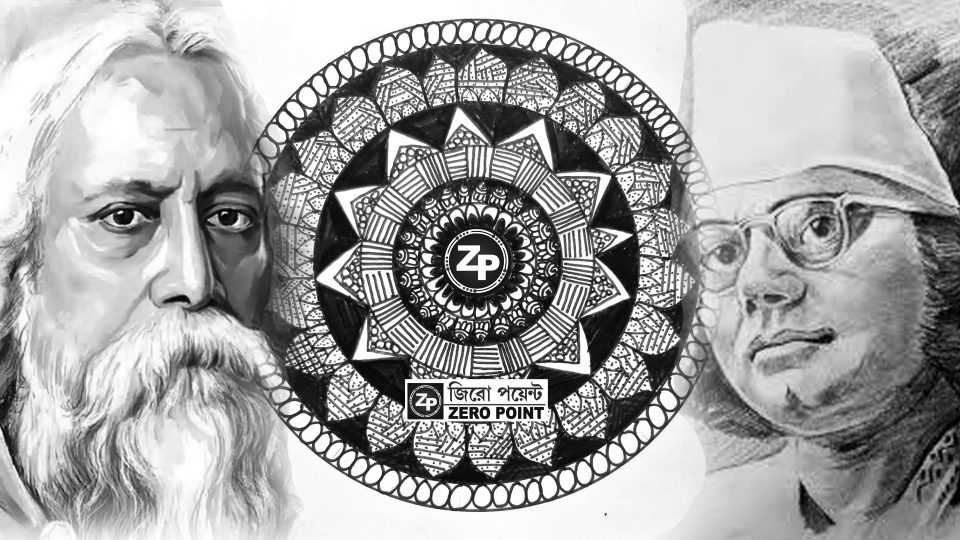
1 টি মন্তব্য
নববর্ষ সংখ্যার পর প্রকাশিত হয়েছে জিরো পয়েন্ট এর মাসিক জৈষ্ঠ্য সংখ্যা “রবীন্দ্র নজরুল সংখ্যা”।
লক ডাউন মাঝে মানুষ যখন গৃহবন্দি তখন রবীন্দ্র নজরুল কে স্মরণ করে জিরো পয়েন্ট এর এই প্রয়াস অতুলনীয়। এই মহান দুই মনীষী দের সম্মান জানানোর পাশাপাশি আমরা এই সংখ্যায় পেলাম অসাধারণ সব সাহিত্য বুনন।
বিশিষ্ট কবি ও বাচিক শিল্পী আরণ্যক বসুর কবিতা সমালোচনা করার মতো ধৃষ্টতা আমার নেই। তাঁর কবিতা মানেই ‘spontaneous overflow of powerful feelings’। ”বৃন্তের দুটি ফুলে” কবিতাটিও ব্যতিক্রম নয়। রবীন্দ্র নজরুল এর পটভূমিকায় তিনি বলেছেন ‘সম্প্রীতি সম্প্রীতি রাখে শান্ত-নিরুদ্বেগ’ ।
শম্পা গাঙ্গুলি ঘোষ এর কবিতা “প্রণমি তোমারে” তে কবিমন রবীন্দ্রময় দৈনন্দিন জীবনের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের ‘আনন্দময় প্রকাশ’ ‘চিরস্থায়ী’ কবির ‘এ হৃদয় মাঝারে’। আঞ্জু মনোয়ারা আনসারী র কবিতা “প্রেম শাশ্বত” তে পাওয়ার অফ আর্ট এর কথা বলা হয়েছে। মানব জীবনের সমস্যাময় পথে বহু বাধা আসবেই। তবু কবির কাছে
‘চির শাশ্বত কবির অমৃত বাণী’ ‘জন্ম জন্মান্তরের তপস্যা ধন’। সৃষ্টি ও স্রষ্টা এই কবিতায় প্রেমময় ঈশ্বর।
তৃতীয় পৃষ্ঠায় শুভাশিস মল্লিক “রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল” শীর্ষক তথ্যপূর্ণ লেখনীতে তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক সম্পর্কে জানা যায়। বদ্রিনাথ পালের লেখা “এক বৃন্তের ফুল” এ অবিনশ্বর রবি-নজরুল কীর্তির জয়গান গেয়েছেন। ” তোমারই খোঁজে” কবিতায় দিকভ্রান্ত কবি ‘জীবনের জয়গান শোনে তোমার থানে বসে।’
কবিরুল এর ছোটগল্প “চন্ডালিকা” অসাধারণ। বর্তমান সময়ের পটভূমিকায় সমাজের নানান বিষয় খুব সুক্ষ চালে তুলে ধরেছেন তিনি। আজকের সমাজে মনিকার খুব দরকার। গল্প টি পড়তে পড়তে ডিলন টমাস এর “A Refusal to Mourn the Death” কবিতাটির কথা মনে পড়লো। আর এই গল্পের মাধ্যমে লেখক সমাজ সচেতনতার পাঠ দিতে ‘reverse psychology’ ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয়।
“আহ্বানে কবি” তে কবি কেতকী মির্জার মননে বিদ্রোহী কবি নজরুলকে ফিরে আসার আর্তি ধরা পড়েছে: ‘ফিরে এসো গো কবি নজরুল/এসো এসো গো তরুন কবি নজরুল’। ডঃ রমলা মুখার্জি র প্রবন্ধ “পত্রিকা সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ” এর বিবরণ পাওয়া যায়। মিরাজুল সেখ “স্মরণে রবীন্দ্রনাথ” ও মুস্তারি বেগমের “অবেলার কবি” কবিতাদুটিতে চিরদার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জয়গান করেছেন।
বাংলা তথা বাঙালির ‘দমবন্ধ বাতাসে কালবৈশাখী’ হলেন কবিগুরু।
“কবিগুরু কে নিয়ে আমার ভাবনা” যে অসীমা সরকার কবিগুরু কে নিয়ে নানান ভাবনা তুলে ধরেছেন। ‘হিরকখন্ড’ উজ্জ্বল রবি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: “অমৃতলোকে থাকো তুমি, হয়ে চির-ভাস্বর,/আমরা সদাই গাহিবো তোমার প্রেমগাঁথা নিরন্তর।” হাস্নে আরা বেগম “চিরনমস্য” কবিতায় বর্তমান সময়ে নজরুল এর অভাব লক্ষ্য করেছেন। তিনি মনে করেন আজকে নজরুল থাকলে ‘বুঝতো সবাই বিদ্রোহ কাকে বলে?’
দেবপ্রিয়া বারিক এর “রঙের রবীন্দ্রনাথ ” এ চিত্রশিল্পী কবিগুরু কে পাওয়া গেলো এবং সঙ্গে বেশ কয়েকটি ছবি। রতন নস্করের “রবিঠাকুর রবিঠাকুর” ও মঞ্জুশ্রী মন্ডলের “বিদ্রোহী কবি” নামক কবিতা দুটিতে যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নজরুল ইসলাম কে সম্মান জানিয়েছেন। “রবীন্দ্র সাহিত্য ও সমাজচেতনা” ই অগ্নিমিত্র রবীন্দ্র সমাজ ভাবনার দিকটি তুলে ধরেছেন। লক ডাউন এর সময় বন্দি জীবনে ‘তোমার (রবীন্দ্র)বাণী, তোমার (রবীন্দ্র) চিন্তায়/গানে গল্পে কবিতায়, দিন কেটে যায়’ বলেছেন কবি বর্ণালী শেঠ তার “আর্জি” কবিতায়। কবি শিলাবৃষ্টি র “সাম্যবাদী” কবিতায় বিদ্রোহী কবি “নজরুল ভারতের প্রতি প্রান্তরে তুমি চির-বিদ্রোহী বীর !” শেষ পাতায় স্থান পেয়েছে অসাধারণ আবৃতিমালা ও পাণ্ডুলিপির ছবি। সব মিলিয়ে খুব সুন্দর লাগলো জৈষ্ঠ্য ১৪২৭ সংখ্যা।
…রজত ঘোষ, বালিন্দর, কালনা, পূর্ব বর্ধমান।